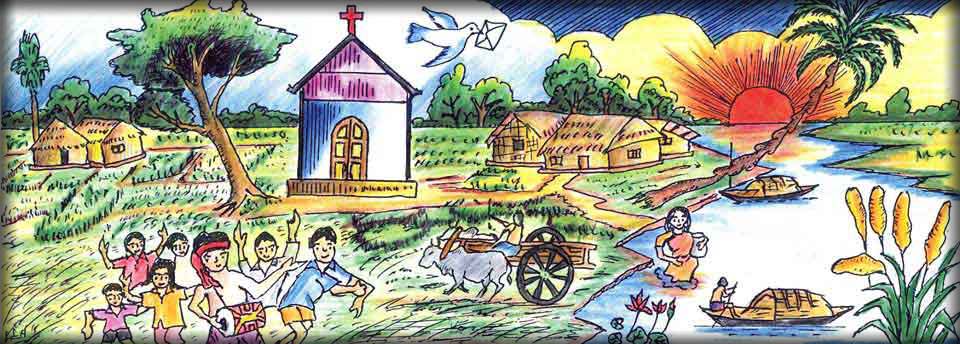রাজশাহী ডাইয়োসিসের ১৭তম পালকীয় সম্মেলনে আলোচনার তালিকায় মূল বিষয় ছিলো- কৃষ্টি/সংস্কৃতির মাধ্যমে খ্রিস্টবাণী প্রচার। দুইশতের অধিকজন প্রতিনিধি নিয়ে এমন একটি আয়োজন অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। তারপর, আদিবাসীও বাঙালি ভাই-বোনদের প্রতি দৃষ্টি রেখে আলোচনার বিষয়বস্তু “কৃষ্টি/সংস্কৃতির মাধ্যমে খ্রিস্টবাণী প্রচার” ছিলো একটা শুভ উদ্যোগ। এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই বাঙালি কৃষ্টির মাধ্যমে চার্চের পালকীয় কাজ চলছে। সুতরাং এই লেখাগুলোতে নতুন করে বাঙালি কৃষ্টি টানতে চাইনা। পালকীয় সভার শেষ পর্যায়ে এসে ‘প্রেরণ বিবৃতি’র মোট ১৮টি সিদ্ধান্তের মধ্যে কমপক্ষে ১০টিই ছিলো কৃষ্টি/সংস্কৃতি নিয়ে, ( সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, সংখ্যা ৩৭, অক্টোবর ৬-১২, ২০১৯, পৃষ্ঠা ২২-২৩)। প্রেরণ বিবৃতির ভূমিকায় বলা হয়েছে, “রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে বসবাসরত বিভিন্ন নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৬টি জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি-সংস্কৃতির ওপর সহভাগীতা ছিল উক্ত কর্মশালার প্রতিপাদ্য বিষয় … কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সকলকে কৃষ্টি-সংস্কৃতির মাধ্যমে মঙ্গলবাণী প্রচারের গুরুত্ব অনুধাবন ও করণীয় এবং কৃষ্টি-সংস্কৃতির মাধ্যমে বাণীপ্রচারের কৌশলসমূহ নির্ধারণে সহায়তা করেছে।” কৃষ্টি/সংস্কৃতি নিয়ে প্রেরণ বিবৃতিতে উল্লেখিত ১০টি সিদ্ধান্তসমূহ আবার তিনটি সার-অংশে সমন্বয় করে আলোচনা করা যেতে পারে। সম্ভাব্য এই তিনটি সার-অংশ হলো ১.কৃষ্টি/সংস্কৃতির চর্চা, শিক্ষা এবং সংরক্ষণ ২. কুসংষ্কার, অপব্যাখ্যা ও অপ-সংস্কৃতি রোধ করে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আনয়ন পদক্ষেপ গ্রহণএবং ৩. নিজস্ব কৃষ্টি/সংস্কৃতির মাধ্যমে উপাসনা ও খ্রিস্টবাণী প্রচার।
কৃষ্টি/সংষ্কৃতির চর্চা, শিক্ষা ও সংরক্ষণ নিয়ে আজকের লেখায় সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করতে চাই। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে, জাতিসংঘের নৃ-তাত্ত্বিক বিষয়ক স্থায়ী ফোরাম তাদের ১৫তম অধিবেশনে উল্লেখ করেছেন যে, “নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী একটি বিশেষ অঞ্চলে আগে বা পরে যখনই বসতী গড়ে তুলুক না কেন, তারা আলাদা জাতিসত্ত্বার-যাদের রাষ্ট্র এবং আর্ন্তজাতিক আইন দ্বারা বিশেষ অধিকার, ভাষা ও ইতিহাস নিশ্চিত করার বিধান থাকবে।” অধিবেশনে আরো বলা হয়, “যেহেতু নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী সুরক্ষিত নয় বরং নানাভাবে তারা রাষ্ট্রকর্তৃক ও ঔপনিবেশ শক্তি কর্তৃক উপেক্ষিত, শোষিত, নির্যাতিত এবং তাদের ওপর রাজনৈতিক শক্তি প্রয়োগ করা হয়- সেহেতু এমন সংখ্যালঘু ব্যক্তি এবং সমাজ যাতে তাদের অঞ্চলে ন্যায্যতা ও অধিকার নিয়ে বসবাস করতে পারে সেই জন্য বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।” তাই প্রথমেই বলতে হয়, একটা নৃ-গোষ্ঠীর কৃষ্টি/সংস্কৃতির চর্চা, শিক্ষা এবং সংরক্ষণের আগে নিশ্চিত থাকতে হবে সে জাতির সুরক্ষা। বসবাসের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা না পাওয়া গেলে আর কোনো কিছ ুচর্চা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।
আজকের আলোচনায় আপাতত: সংক্ষিপ্তভাবে নজর দিতে চাই- কৃষ্টি/সংস্কৃতির চর্চা, শিক্ষা এবং সংরক্ষণের দিকে। বাংলাদেশের জাতীয় দিবসগুলোতে যদি আদিবাসীতে অংশগ্রহণ থাকে, তবে দর্শকদের সমাগম বেড়ে যায়। চিরাচরিত বাংলা সংস্কৃতির বাইরে দর্শকগণ ভিন্ন কিছু দেখতে চান। আদিবাসীদের উপস্থাপনার মধ্যে থাকে বৈচিত্রতা, যেমন- বাহারী সাজগোছ ও পোশাক, বাদ্যযন্ত্রের তাল-লয়-সঙ্গীত এবং ছন্দের নিখুঁত ঝুমুর। সবকিছু মিলে একটা আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশ তৈরি হয়। মাত্র কয়েক দিনের চর্চায় এমন একটা উপস্থাপনা দাঁড়িয়ে যায়। আর যদি নিয়মিত চর্চা হয় তাহলে বৈচিত্র্যতা আরো বৃদ্ধি পাবে।
সংস্কৃতি চর্চার বিষয় বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে ভাষা সংরক্ষণ। পারিবারিকভাবে ভাষার চর্চা অবশ্যই থাকতে হবে তবে সেটাই ভাষার ক্ষার যথেষ্ট উপায় নয়। মৌখিক চর্চার পাশাপাশি প্রকাশনা সুবিধা থাকতে হবে। সুবিধামতো বর্ণমালা দিয়ে ব্যাকরণ মেনে প্রকাশ করতে হবে পাঠ্যবই, সাময়িকী ও ভাষা শিক্ষার পর্ব। প্রকাশনা সুবিধা ছাড়া ভাষা রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এই নিয়ে আজকাল আদিবাসী শিক্ষিত সমাজে মেলা কথাবার্তা হয় কিন্তু কাজের কাজটি তেমন হচ্ছে না। আদিবাসীদের মধ্যে এখন অনেক শিক্ষিত হয়েছেন, অনেক ফাদার-সিস্টার হয়েছেন। তাদের অনেকে শহরে বন্দরে, চার্চে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। কিন্তু তারা নিজ সমাজের জন্য, ভাষা-কৃষ্টি রক্ষার জন্য কতোটুকু সময় দিচ্ছেন, সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং ভাবনার বিষয়। একজন বাঙালি হিসেবে এই অভাবটা চোখে পড়ে। এক দুই দিনের দুই/একটি সেমিনার করে, বক্তৃতা দিয়ে এগুলো সম্ভব নয়। আর এটাকে চর্চাও বলা যাবে না। চর্চা খণ্ডকালীন নয়, এটাএকটা দীর্ঘমেয়াদী টেকসই পরিকল্পনা, অনুশীলন ও অনুকরণ। মনে রাখতে হবে, একটা জাতিকে ধ্বংস করতে হলে- শিক্ষাকে বলি দেওয়া যেমন যথেষ্ট- তেমনি একটি নৃ-তাত্ত্বিক জাতি স্বকীয়তা হারাতে পারে ভাষা-কৃষ্টি হারিয়ে। উত্তরবঙ্গের কয়েকটি আদিবাসী তাদের ভাষা বাংলা হরফে লিখবেন নাকী রোমান হরফে লিখবেন, এখনো এই বিতর্কের মধ্যেই আটকে আছেন।
কৃষ্টি/সংস্কৃতির চর্চা, শিক্ষা এবং সংরক্ষণের তাগিদটা শিক্ষিতদের কাছ থেকে আসতে হবে, তাদের গবেষণা করে প্রয়োজনের আঙ্গীকারগুলো চিহ্নিত করতে হবে। এক সময় প্রবীণরা কৃষ্টি/সংস্কৃতি এবং ভাষা ভালোই জানতেন। তখন আজকের মতো বাইরের প্রভাব ছিলো না। এখন দিন পাল্টে গেছে। আকাশ সংস্কৃতি ও আধুনিকতার কারণে উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা। তাই প্রবীণদের পক্ষে আজ অনেক কিছু সম্ভব নয়। তবে এখনো প্রবীণরা কৃষ্টি/সংস্কৃতির অনেক কিছ ুজানেন- যেগুলো উদ্ধার করার দায়িত্ব শিক্ষিতদের।
শুধু মাত্র চার্চ উদ্যোগ নিলে হবেনা। চার্চের ভুমিকা থাকবে তাদের উদ্যোগগুলো ধরে ধরে এগুনো, সহায়তা ও সমর্থন দেওয়া। চার্চ নিজে থেকে উদ্যোগ নিলে এক সময় হতে পারে বলতে শোনা যাবে ভাষা, কৃষ্টি/সংস্কৃতি রক্ষার নামে চার্চ সব ধ্বংস করছে। জোর দিয়েই বলতে চাই- উদ্যোগ আসতে হবে আদিবাসীদের তরফ থেকে। উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে বলতে চাই- এই কাজটি করতে গিয়ে আদিবাসীদের উচিৎ হবে রিসোর্স পারশন হিসেবে বাঙালিদের সম্পৃক্ত করা। প্রাসঙ্গিক কারণে এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, আদিবাসীদের নিয়ে যতো গবেষণা, বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, তার সিংহভাগ করেছেন নন-আদিবাসী লেখকরা। (চলবে)
ফাদার সুনীল রোজারিও
কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মাধ্যমে খ্রিস্টবাণী প্রচার- ৩
Please follow and like us: